বাংলাদেশও কি তবে যুদ্ধে জড়াচ্ছে?
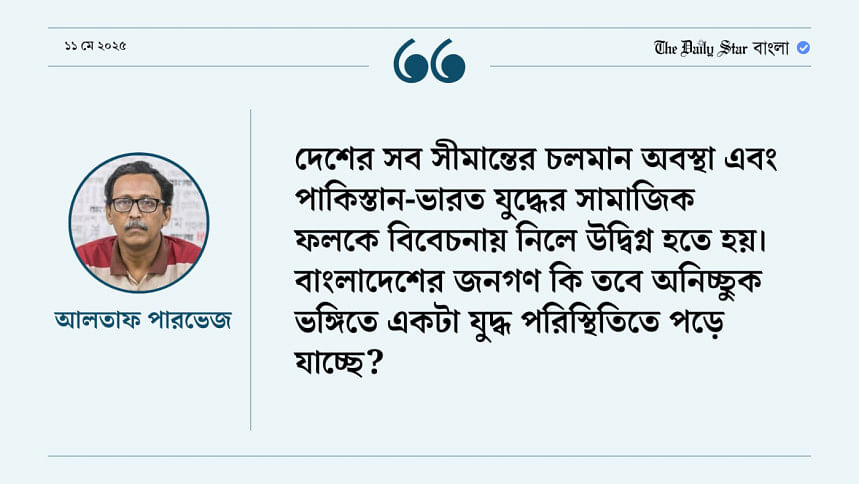
পাকিস্তান ও ভারত আবার একটা যুদ্ধের ভেতর ঢুকেছে। অতীতে তিনবার যুদ্ধ করেছে তারা। সেসব যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বলছে, এই দুই দেশের যুদ্ধ তাদের সীমানায় সীমিত থাকে না। তার আঁচ ছড়ায় বাংলাদেশেও। ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যাচের মতো ওই উভয়ের গোলাগুলিতেও মানসিকভাবে নিরপেক্ষ বা নির্মোহ থাকতে পারেন না বাংলাদেশ-সমাজ।
এটা কেবল ধর্মের কারণে ঘটে না, ভৌগলিক অতীতের কারণেও হয়। যা আবার পুরোপুরি অতীত হয়েও যায়নি। সামাজিক স্তরে অবস্থাটা অনেক সময় এমনই মনে হয় যে, বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারত যেন পারস্পরিক ঝগড়ায় লিপ্ত একটা যৌথ পরিবার। 'অতীত' এই তিন সমাজকে রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত করেছে, কিন্তু পৃথক 'বর্তমান' তাদের নিরাসক্ত করতে পারেনি।
ফলে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব সীমান্তে যত রক্ত ঝরবে, বাংলাদেশও তত তেতে উঠবে। যুদ্ধের প্রথম দিনই দেশের প্রধান কাগজে কাজ করা বন্ধু জানালেন তাদের 'ভিউয়ার' তিনগুণ বেড়েছে।
পাকিস্তানে গোলা ছোঁড়ার পাশাপাশি ভারত যুদ্ধের প্রথম দিনই তার আঁচ ছড়িয়েছে বাংলাদেশ সীমান্তেও ব্যাপকভাবে 'পুশইন' কর্মসূচি নিয়ে। ৮ মে এই লেখা তৈরির সময় খাগড়াছড়ি, মৌলভীবাজার, কুড়িগ্রামসহ অনেক সীমান্তে
ভারত তার দেশের নাগরিকদের বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। শত শত মানুষকে ইতোমধ্যে তারা পুশইন করতে সমর্থ হয়েছে।
দরিদ্র প্রকৃতির এই মানুষদের একাংশ বাংলাভাষী এবং তাদের গুজরাট অঞ্চল থেকে ধরে এনে বাংলাদেশে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো—বাংলাভাষী হলেই কি কেউ বাংলাদেশি হয়ে যায়? আর, ভারতে যদি অবৈধভাবে কোনো বাংলাদেশি থাকেন, সেই বিষয়ে কূটনৈতিক চ্যানেলে কথাবার্তা বলা যেতো। তার বদলে যেভাবে সীমান্তের অনেকগুলো জায়গা দিয়ে একযোগে পুশইন কর্মসূচি নেওয়া হলো, তা উসকানিমূলক।
ইতোমধ্যে পুশইনে ঢুকিয়ে দেওয়া মানুষরা এও বলছেন, সীমান্তের ওদিকে ভারতের বিভিন্ন সংস্থা আরও বাংলাভাষীদের জড়ো করছে। আরাকান থেকে ভারতে যাওয়া অনেক রোহিঙ্গাদের জড়ো করা হয়েছে বাংলাদেশে পুশইন করার জন্য। তথ্য হিসেবে এসব অতি উদ্বেগজনক। এরকম পদক্ষেপ যে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণকে চাপে ফেলবে, ক্ষুব্ধ করবে সেটা ভারতের নীতিনির্ধারকদের না বোঝার কারণ নেই।
পুশইন সামাল দিতে নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের সামনে পুশব্যাক কর্মসূচি গ্রহণের বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। সেটা অমানবিক হলেও বাংলাদেশ সরকারের সামনে এক্ষেত্রে কোনো বিকল্প থাকছে না। পাল্টাপাল্টি পুশইন ও পুশব্যাক সীমান্ত পরিস্থিতিকে উত্তপ্ত করতে বাধ্য। সে কারণেই জনমনে প্রশ্ন উঠেছে, ভারত কি তবে পাকিস্তান সীমান্তের মতো বাংলাদেশ সীমান্তেও উত্তেজনা ছড়াতে চায়?
এই প্রশ্নটি এ কারণেও গুরুত্বপূর্ণ, গত ৭-৮ মাস ধরে বাংলাদেশ ভারতের ভেতর থেকে অকল্পনীয় এক প্রচারযুদ্ধের শিকার। বাংলাদেশে কী ধরনের সরকার থাকবে সেটা একান্তই বাংলাদেশের মানুষের পছন্দের ব্যাপার। এখানকার রাজনৈতিক পটপরিবর্তনকে ভারত সরকার তার জন্য সুখকর মনে না করার কারণ থাকতে পারে। কিন্তু সেজন্য পুরো দেশকে এবং এখানকার সব মানুষকে জড়িয়ে লাগাতার অসত্য প্রচারণাকে এক ধরনের পদ্ধতিগত বৈরিতা হিসেবে দেখার অবকাশ রয়েছে। এরকম বৈরিতাকে নরম ধাঁচের যুদ্ধকৌশল হিসেবেও দেখা যায়।
ভারতের দিক থেকে ক্রমাগত এরকম বৈরী প্রচারণা এবং ব্যাপক হারে পুশইন চেষ্টার পাশাপাশি দক্ষিণ সীমান্তেও উত্তেজনাকর এক অবস্থায় পড়েছে বাংলাদেশ।
অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে আরাকান থেকে নতুন করে রোহিঙ্গাদের অবৈধভাবে বাংলাদেশে প্রবেশ বেশ বেড়ে গেছে। গত ৭-৮ মাসে লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা নতুন করে বাংলাদেশে প্রবেশ করায় আশ্রয় শিবিরগুলোতে এই জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ১৩ লাখে দাঁড়িয়েছে। আশ্রয়ের খোঁজে আসা নতুন-পুরোনো এই মানুষদের নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগের একটা বড় কারণ এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক আর্থিক সহায়তা কমে আসার আলামত।
এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠেছে—আরাকান থেকে নতুন করে রোহিঙ্গা ঢল শুরু হলো কেন? নতুন শরণার্থী দল বলছে, আরাকান আর্মির রাখাইন গেরিলাদের তরফ থেকে তাদের জন্য নিরাপত্তাহীনতার চাপ তৈরি হয়েছে।
আরাকান আর্মি ইতোমধ্যে আরাকান প্রদেশের প্রায় ৮০ ভাগ এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়েছে। তবে মিয়ানমার সেনাবাহিনী 'তাতমা-দ' আরাকানের বিভিন্ন স্থানে বোমাবর্ষণও থামাচ্ছে না। এরকম যুদ্ধ পরিস্থিতি সেখানে মানবিক ও নিরাপত্তা সংকট তৈরি করছে। তার উত্তর হিসেবে জাতিসংঘ সম্প্রতি বাংলাদেশকে অনুরোধ করেছে আরাকান অভিমুখী একটা 'করিডোর' বা 'চ্যানেল' খুলে দেওয়ার জন্য, যা দিয়ে তারা আরাকানে 'আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তা' পাঠাতে চায়।
যুদ্ধরত জনপদে বা যুদ্ধবিধ্বস্ত লোকালয়ে অপর কোনো দেশ থেকে এরকম 'চ্যানেল' প্রতিষ্ঠার পূর্ব-নজির আছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে গাজা বা ইউক্রেনে সেরকম উদ্যোগ নিয়েছিল জাতিসংঘ। কিন্তু সেসব অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। ওই উদ্যোগগুলো লক্ষ্য পূরণে সফল হয়নি। সেরকম বিরূপ অভিজ্ঞতার কারণে বাংলাদেশেও আরাকানমুখী করিডোর প্রস্তাব শুরু থেকে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। অনেকগুলো প্রশ্ন উঠেছে এ নিয়ে। যেমন: এই করিডোরের ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ বা জাতিসংঘ—কার হাতে থাকবে? এই চ্যানেল দিয়ে কী ধরনের পণ্য যাবে এবং তার বিলিবণ্টনে কি রোহিঙ্গারাও যুক্ত থাকবে? সবচেয়ে বড় বিষয় এই চ্যানেলের নিরাপত্তা প্রশ্ন।
এই চ্যানেল বিষয়ে মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী যদি রাজি না থাকে বা চীন-ভারতের কারো আপত্তি থাকলে একে সুরক্ষা দেবে কে এবং সেই সুরক্ষার জন্য 'নো-ফ্লাই জোন' জাতীয় কিছু হবে কি না?
নো-ফ্লাই জোনসহ করিডোরের নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলোর সঙ্গে সামরিক ব্যাপারও জড়িয়ে আছে, যা স্পর্শকাতর। দেশে পার্লামেন্ট থাকলে এ বিষয়গুলো নিয়ে নিশ্চিতভাবে জনপ্রতিনিধিরা কথা বলতেন। কিন্তু অন্তর্বর্তী সরকার স্পর্শকাতর এ বিষয়ে রাজনীতিবিদদের সঙ্গেও আলোচনা করেনি বলেই মনে হচ্ছে।
সরকারের ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিরা এই চ্যানেল নিয়ে কিছু স্ববিরোধী বক্তব্যও দিয়েছেন। প্রথমে একজন উপদেষ্টা বলেছেন, সরকার করিডোরের প্রস্তাবে নীতিগতভাবে রাজি হয়েছে, তবে কিছু শর্ত দিয়েছে। আরেকজন কর্তা বলেছেন, এ নিয়ে কোনো আলোচনাই হয়নি। তৃতীয় পর্যায়ে সরকারি তরফ থেকে বলা হচ্ছে, করিডোর নয়, সরকার একটা চ্যানেলের কথা বিবেচনা করছে। অসমন্বিত ও বিরোধাত্মক এসব বক্তব্যে জনমনে এই মর্মে উদ্বেগ বাড়ছে যে, বাংলাদেশ তার দক্ষিণ সীমান্তে সামরিক ধাঁচের কোনো উদ্যোগে জড়াচ্ছে কি না।
মিয়ানমার ও আরাকানের বেলায় বাংলাদেশের প্রধান অগ্রাধিকার নিশ্চিতভাবে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠানো এবং তাদের আসা বন্ধ করা। আরাকানের এখনকার যে অবস্থা তাতে সেখানে রোহিঙ্গাদের ফেরত পাঠাতে হলে আরাকান আর্মির সম্মতি ও অংশগ্রহণ লাগবে। আবার যেহেতু মিয়ানমার দেশ হিসেবে এখনো অস্তিত্বশীল এবং নেপিদোতে একটা সরকার আছে, সুতরাং আরাকানে চ্যানেল করতে হলে তাদেরও সম্মতি লাগবে। এরকম সব পক্ষ সম্মত হলেই কেবল মানবিক ত্রাণের বিষয় বিবেচনা করা যায়। সেই বিবেচনায় অবশ্যই প্রধান শর্ত থাকতে হবে রোহিঙ্গাদের ফেরতের প্রশ্ন। কিন্তু সর্বশেষ উদ্যোগে সে বিষয়টি যুক্ত আছে কি না তা জানা যাচ্ছে না। জাতীয়ভাবে অতিগুরুত্বপূর্ণ এবং সামরিক দিক থেকে অতি স্পর্শকাতর এই বিষয়ে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে যদি যথেষ্ট মতবিনিময় করা না হয়, তাহলে সেটা ভবিষ্যতে দেশে বিতর্ক ও দ্বিধাবিভক্তি বাড়াবে।
সামরিক ধাঁচের আন্তঃদেশীয় কোনো প্রকল্পে জাতীয় ঐকমত্য ছাড়া যুক্ত হওয়া অবশ্যই একটা ঝুঁকি। প্রশ্ন হলো—একাএকা এরকম ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার বর্তমান সরকারের আছে কি না।
গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে গঠিত এই সরকারের পেছনে জনগণের সমর্থন থাকলেও এটা অনির্বাচিত সরকার। আবার পাশাপাশি দেশে বর্তমানে তীব্র রাজনৈতিক টানাপোড়েন চলছে। নির্বাচন কবে হবে এ নিয়ে অনিশ্চয়তা ছড়াচ্ছে। এরকম অবস্থায় আরাকানের দিকে মানবিক চ্যানেল দেওয়ার বিষয় নির্বাচনকেন্দ্রীক অনিশ্চয়তায় বাড়তি উপাদান হয়ে গেছে। তাছাড়া, সীমান্তে করিডোরের সামরিক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও হতে পারে যেকোনো সময়। সবমিলে দেশের সব সীমান্তের চলমান অবস্থা এবং পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সামাজিক ফলকে বিবেচনায় নিলে উদ্বিগ্ন হতে হয়। বাংলাদেশের জনগণ কি তবে অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে একটা যুদ্ধ পরিস্থিতিতে পড়ে যাচ্ছে? নাকি ইতোমধ্যে জড়িয়ে গেছে? নির্বাচনহীন, জনপ্রতিনিধিহীন সমাজে এসব প্রশ্নের উত্তর কে দিবে?
আলতাফ পারভেজ: দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক









Comments