পছন্দের বিভাগ এবং আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলাদেশে শিক্ষাঙ্গনে খুবই পরিচিত বিষয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পছন্দের বিভাগ না পাওয়া। প্রায়ই আমি কিছু লেখা পড়ি, যার মূল বিষয় পছন্দের বিষয় না পেয়ে শিক্ষার্থীদের হতাশাগ্রস্ত হয়ে যাওয়া। এরপর পড়ালেখা থেকে মন উঠে যাওয়া এবং বলতে গেলে ক্যারিয়ারের সমাপ্তি।
এ ছাড়াও আপনার ভর্তি হওয়া পছন্দের বিষয়টির যদি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বাজার দর না থাকে, আপনার পরিচিত মানুষই আপনার জীবন বিষিয়ে তুলবে। সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের একটি গ্রুপে পড়লাম একজন ছাত্রী পছন্দ করে দর্শন বিভাগে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু অন্য বিভাগের একজন শিক্ষকের মন্তব্যের কারণে বিষয়টি থেকে তার মন উঠে যায়। নিজের পছন্দের বিষয়ে পড়তে না পারার তীব্র হতাশায় ভোগা অনেক শিক্ষার্থীকে আমি ঝরে যেতে দেখেছি বিজ্ঞান অনুষদে।
এ ছাড়া আমাদের সমাজ, বাবা-মার প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের জীবন বিষিয়ে তোলে। উন্নত বিশ্বে হাইস্কুল, যা আমাদের ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, শেষ হওয়ার আগেই শিক্ষার্থীরা আগে থেকেই জানে তারা কি পড়তে চায়। সেখানে স্কুলে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং আছে। তাই হাইস্কুলে ওঠার পর তারা আগে থেকেই পরিকল্পনা করে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে, কোন বিভাগে পড়বে, কীভাবে আগাবে। বাংলাদেশে ১৮ বছর বয়সী এই ছেলে-মেয়েদের জীবনের লক্ষ্য হচ্ছে বাবা-মার প্রত্যাশা। তাদের নিজস্ব পছন্দের ওপর আত্মবিশ্বাস থাকে না। বাবা-মার আত্মবিশ্বাস নিয়েই তারা বড় হয়। প্রচণ্ড ভালো শিক্ষার্থীও নিজের পছন্দসই বিভাগে পড়ে না এবং এক গ্রুপ প্রতিযোগিতা পূর্ণ পরীক্ষায় নিজের পছন্দসই বিষয় না পেয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়। বিজ্ঞান অনুষদে তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। যদিও উন্নত দেশে অনেক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই বিভাগ নির্ধারণ করে না। তাদেরকে আমরা আন-ডিসাইডেড বলি। তাদের দুই সেমিস্টার বা আরও একটু বেশি সময় দেওয়া হয় নিজের পছন্দমতো বিভাগ নির্ধারণ করতে। এ ছাড়া চাইলেই তারা বিভাগই পরিবর্তন করতে পারে। কেউ যদি পদার্থ বিজ্ঞানে ভর্তি হয় এবং এক বছর পর বুঝতে পারে যে সে রসায়ন নিয়ে পড়তে চায়, বাংলাদেশে তা আর সম্ভব নয়। কিন্তু এই শিক্ষার্থী সারা জীবন এই দুঃখ নিয়ে তার জীবন পার করবে।
আমি আমেরিকাতে অ্যাকাডেমিক পরিমণ্ডলে আছি বলে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমার কিছু অভিজ্ঞতা সবসময় শেয়ার করার চেষ্টা করি। আমি তখন ফ্লোরিডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্স করছি। আমি জৈব রসায়নের তৃতীয় সেমিস্টারের একটা ল্যাব টিএ হিসেবে কাজ করি। আমার ক্লাস ছিল বিকালে। ঝাঁকড়া চুলওয়ালা এক লম্বা ছেলেকে একটা ল্যাব পেপারে তাকে একটু কম নম্বর দিয়েছিলাম। সে এসে আমাকে বলল, 'দেখ আমি মেডিকেলে পড়তে চাই। আমার ভুলগুলো আমাকে ব্যাখ্যা করো, যাতে আমি দ্বিতীয় বার এই ভুল না করি। আমার খুব ভালো গ্রেড দরকার।' কথাচ্ছলে সে বলল, সে আসলে এখানকার একজন ইন্সট্রাক্টর। আমি তো অবাক। মানে সে এখানে লেকচারার সমপর্যায়ের একজন শিক্ষক এবং তার পিএইচডি আছে। সে আরও বলল, 'আসলে আমি মেডিকেল অ্যানথ্রপলজি নামে একটা কোর্স পড়াই এবং এটা পড়াতে গিয়ে আমার মনে হয়েছ, আমি পেশা পরিবর্তন করে ডাক্তার হতে চাই। আমার যেহেতু বিজ্ঞানের আন্ডার গ্র্যাজুয়েটের অনেকগুলো কোর্স করা নেই, তাই আমি পার্টটাইমে এই কোর্সগুলো করে নিচ্ছি।' আমি ভাবলাম, হায়রে দেশ! কিন্তু আমার মাথা আরও ঘুরে যাওয়ার অবস্থা হলো যখন এক মেয়ে জানালো, সে মিউজিকে পিএইচডি করেছে এবং একটি মেডিকেল স্কুলে ভর্তির জন্য সে নির্বাচিত হয়েছে। কিন্তু তার ইচ্ছা এর থেকেও বড় আরেকটি স্কুলে সে যাবে। তাই সে এই উচ্চতর কোর্সটি করছে। এই রকম অনেক শিক্ষার্থী আমি দেখেছি একটা ডিগ্রি নিয়ে সম্পূর্ণ ইউটার্ন নিয়ে অন্য বিষয় পড়ছে। যাদের আমেরিকার পড়াশোনা সম্পর্কে ধারনা নেই তাদের জন্য বলছি, এখানে ডাক্তারি ও আইন বিষয়ের মতো প্রফেশনাল বিষয়গুলো পড়তে গেলে প্রথমে ব্যাচেলর ডিগ্রী করতে হয়। আমাদের সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় ঘ বিভাগটি থাকাতে অনেকে বিজ্ঞান থেকে মানবিক এবং বাণিজ্য বিভাগে পড়ছে। কিন্তু তারা একবার সরে গেলে আবার ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে বিভাগ পরিবর্তন ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।
আমার সবচেয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় যখন আমি রিসার্চ ফেলো হিসেবে আমেরিকার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব হেলথের আন্ডারে ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব এনভায়রনমেন্টাল হেলথ সায়েন্স ইন্সটিটিউটে গবেষণা করতে যাই। আমার বস ছিলেন একজন এমডি। তিনি ছিলেন আমেরিকান ইহুদি, পেশায় একজন ফুসফুসের ডাক্তার, পরিপূর্ণ ভাবে এখন একজন বিজ্ঞানী। বছরে একমাসের জন্য ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি বিভাগে প্র্যাকটিস করতেন। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, তার বায়ো দেখলে সবার মাথা ঘুরবে। সে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিলসফিতে গ্রাজুয়েশন করেছে এবং এমডি করেছে হার্ভার্ড থেকে। এরপর রেসিডেন্সি করেছে ম্যাসাচুসেটস জেনারেল হাসপাতালে এবং পরবর্তীতে ফুসফুস সংক্রান্ত বিষয়ে ফেলোশিপ করেছে কলোরাডো বিশ্ববিদ্যালয়ে। একবার একসঙ্গে দুপুরের খাবার খাওয়ার সময় তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি ফিলসফি কেন পড়তে গেলে? বলল, 'দেখ আমার বাবা ডাক্তার ছিলেন, আমি প্রথমে কি পড়ব তা বুঝতে পারিনি। ফিলসফি ভালো লাগত। আমি শুধু অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছি আমার কী ভালো লাগে। পরে আমার মনে হয়েছে, ডাক্তারি পড়ি এবং বিজ্ঞানের অতিরিক্ত কোর্সগুলো করে হার্ভার্ডে এমডি করলাম। এরপর রেসিডেন্সি এবং ফেলোশিপের পর আমার মনে হয়েছে, বায়ো মেডিকেল গবেষণা আমার জন্য যথার্থ। তাই আমি পুরোটাই মন দিয়েছি এটাতে। আমি শুনে বিষণ্ণ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি সেশনজটের কারণে চার বছরের ডিগ্রী আট বছরে শেষ করেছি। সে সময়ে একটা পিএইচডি করা যায়। আমার পিএইচডির সময় আমার প্রফেসরের বয়স আমার থেকে খুব বেশি ছিল না। আমরা কতো পিছিয়ে যাই। যদিও আমার ভাগ্য সঠিক বিষয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে। বিষয়ের ভেতরে থেকে আমাকে অনেকদিন অনুসন্ধান করতে হয়েছে আমি কি চাই। আমাদের সেশনজটগুলো কী বেদনাদায়ক সেটা উন্নত বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে না আসলে বোঝা যায় না।
যাই হোক, হা হুতাশ করে লিখে কোনো লাভ নেই। আমি সবসময়ে চেষ্টা করি কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিতে। আমার সঙ্গে কেউ একমত হতে পারে অথবা নাও হতে পারে। উন্নত বিশ্বে বিষয় পরিবর্তন করা যায়। কারণ এখানে প্রচুর বিশ্ববিদ্যালয় আছে। কারও যদি প্রকৌশল পড়ার মতো মেধা থাকে, সে চাইলে সেটা পড়তে পারে। কিন্তু, বাংলাদেশে চাইলেও পড়া যায় না। কারণ আমাদের শিক্ষার্থী অনেক বেশি এবং বিশ্ববিদ্যালয় অনেক কম।
বাংলাদেশে এখন অনেক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা সরকার নিয়েছে। এর বেশ কিছু ভালো দিক রয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিষয়গুলোতে উচ্চশিক্ষার অনেক সুযোগ উন্নত বিশ্বে আছে। এই দক্ষ জনশক্তির এক ভাগও যদি দেশে ফিরে আসে, তা দেশের জন্য লাভজনক। কিন্তু তাদেরকে দেশে ফিরিয়ে আনার পরিবেশটাও দিতে হবে। খারাপ দিকটা হচ্ছে, মান ঠিক না করে বিশ্ববিদ্যালয় যত্রতত্র করাও ঠিক নয়। তা লাভের থেকে ক্ষতিই করবে বেশি। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গুলো এবং তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করা দরকার।
লেখার মূল বিষয়, পছন্দের বিভাগে ফেরত আসি। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে শিক্ষার্থী বান্ধব সহজেই কিছু ব্যবস্থা নেওয়া যায়। সেমিস্টার পদ্ধতিতে এটা করা খুব সহজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ১০ শতাংশ শিক্ষার্থী প্রতিটি বিভাগে আনডিসাইডেড রাখতে পারে। তারা যে বিভাগে ভর্তি হবে, সেই বিভাগ ছাড়া অন্য যে বিভাগ ভালো লাগবে সেখানে দুটি কোর্স করতে পারে। কোর্স পারফরমেন্স অনুযায়ী ভালো লাগলে আনডিসাইডেড থেকে ডিসাইডেড হিসেবে মেধা অনুযায়ী বিভাগ পরিবর্তন করার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।
এ ছাড়া আরেকটি বিষয় আছে। এখানে আমরা বলি মেজর এবং মাইনর বিষয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা যখন পড়েছি, আমাদের ছিল সাবসিডিয়ারি। আমার সাবসিডিয়ারি ছিল পদার্থ বিজ্ঞান এবং গণিত। আমাদের সময়ে এটা পাশ করলেই হয়ে যেত। এখন এর পরিবর্তন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ডাবল মেজর করার জন্য সুযোগ দেয় না। পরিস্থিতি বিবেচনা করলে সেটা হয়ত ঠিক আছে। কিন্তু সহজেই মাইনর ব্যাপারটাকে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব। কেউ চাইলে তার বিভাগের প্রয়োজনীয় কোর্সের বাইরে অন্য একটি বিষয়ে মাইনর করতে পারে। এর জন্য তাকে বেশ কিছু কোর্স সেই বিষয়ের ওপর নিতে হবে। কেউ হয়ত রসায়ন পড়ছে, তার হয়ত প্রোগ্রামিং করতে ভালো লাগে। সে কম্পিউটার সায়েন্সে মাইনর করতে পারে। এই আধুনিক বিশ্বে সব কিছুই এখন ইন্টার ডিসিপ্লিনারি এবং এটা শিক্ষার্থীদের জন্য কি পরিমাণ উপযোগী হবে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। এ ছাড়া শিক্ষার্থীরা চাইলে মাইনর বিষয়ের ওপর পরবর্তীতে একটি মাস্টার্স করলেই সে তার কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে পারবে।
আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার পদ্ধতি শিক্ষার্থী বান্ধব নয়। আমাদের দেশে একবার বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ না পেলে তার সারা জীবন শেষ। অথচ উন্নত বিশ্বে কমিউনিটি কলেজে দুই বছর পড়ে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার পড়তে আসতে পারে। আমরা চাইলে সহজেই দুবছর পর আবার একটা পরীক্ষা দিয়ে ওই পর্যায়ে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ দিতে পারি।
আমেরিকাতে ডাক্তারি ও আইন পেশার জন্য প্রথমে ব্যাচেলর ডিগ্রী প্রয়োজন হয়। এরপর তারা বেশ কয়েকবার সুযোগ পায় ভর্তি পরীক্ষাগুলো দেওয়ার জন্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞ তৈরি করা। এরপর তারা কর্মক্ষেত্র বেছে নিবে তার পছন্দ অনুযায়ী। কিন্তু পছন্দের বিষয়ে পড়তে না পেরে যে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী হতাশায় ভুগে জীবন নষ্ট করেছে, তা থেকে উত্তরণের জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। একটি শিক্ষার্থী বান্ধব বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা তেমন কঠিন নয়। এর জন্য দরকার সদিচ্ছা, কিছু পরিকল্পনা এবং ধীরে ধীরে এর বাস্তবায়ন। একটি আধুনিক একুশ শতকের বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উন্নতি করুক, প্রবাসে থেকেও আমরা সেটা আশা করি।
সাইফুল মাহমুদ চৌধুরী: যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এট আরলিংটনের রসায়ন এবং প্রাণ রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)




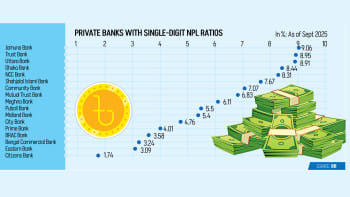
Comments