মাছ চাষে নীরব বিপ্লব, উদ্বেগ অ্যান্টিবায়োটিক-রাসায়নিকের অপব্যবহার

জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় বাংলাদেশের বিপুল জলাশয় হারিয়ে গেছে। বছরের পর বছর মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করা জেলেরা ধীরে ধীরে মাছ কম পাচ্ছেন। তারপরও এ দেশের গ্রামীণ জনপদে সেই পুরোনো প্রবাদ—মাছে ভাতে বাঙালি—আজও টিকে আছে।
তারা এখন পুকুর খনন করেছেন, ছোট ছোট হ্যাচারিতে কোমর পানিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকছেন, আর ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছেন এক সমৃদ্ধশালী শিল্প। তাদের এই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাঙালির ভাতের থালা থেকে মাছ আজও হারিয়ে যায়নি।
এমন নিরন্তর প্রচেষ্টা আর উদ্যোগের গল্প ছড়িয়ে আছে দেশের প্রায় প্রতিটি গ্রামেগঞ্জে।

বাংলাদেশে মাছচাষে নীরব বিপ্লব
উদাহরণ হিসেবে আব্দুল জলিল বকুলকেই ধরা যাক। ১৭ বছর আগে তিনি ময়মনসিংহের একটি গ্রামে ফুটবল মাঠ আকারের জমিতে দুটি পুকুর খনন করেছিলেন। আনন্দিপুরের স্থানীয়রা তখন তাকে পাগল মনে করেছিলেন।
কিন্তু আজ ৫৬ বছর বয়সী বকুল ৩৫ একর জমিতে ২৫টি পুকুরে কার্প, পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া মাছ চাষ করেন।
শুরুর দিকে ময়মনসিংহের আশপাশের হ্যাচারি থেকে মাছের পোনা সংগ্রহ করতেন বকুল। মাছের খাবার আনতেন ভালুকা উপজেলা থেকে এবং ঢাকার বাজারে মাছ বিক্রি করতেন। পরে রাজধানীর ব্যবসায়ীরাই সরাসরি তার খামারে যেতে শুরু করে মাছ কিনতে।
পুকুর পেলে ব্যবসা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে বকুলের।
গত এক দশকে একটি পুকুর থেকে নিজের খামার পাঁচটি পুকুরে পরিণত করেছেন আনন্দিপুরের আরেক বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন।
বকুল ও আনোয়ারের মতো কৃষকের প্রচেষ্টায় মাছ চাষ এখন জাতীয় শিল্পে রূপ নিয়েছে—কোটি মানুষের আহার জোগাচ্ছে, লাখো মানুষের কর্মসংস্থান তৈরি করেছে এবং বাংলাদেশকে বিশ্বের শীর্ষ মাছ উৎপাদনকারীদের কাতারে দাঁড় করিয়েছে।

শীর্ষে খামারভিত্তিক মাছচাষ
সরকারি তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশে ৫০ লাখ টনেরও বেশি মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এর প্রায় ৬০ শতাংশ এসেছে খামারভিত্তিক চাষ থেকে, যেখানে ১৯৮০-এর দশকের শুরুতে এ হার ছিল মাত্র ১৬ শতাংশ।
একসময় নদী, হাওর ও প্লাবনভূমি থেকে দেশের মোট মাছের চাহিদার দুই-তৃতীয়াংশ পূরণ হতো। এখন দিন বদলে গেছে। এসব উৎস থেকে মোট উৎপাদন প্রায় একই থাকলেও চাহিদার মাত্র ২৮ শতাংশ পূরণ হচ্ছে।
বাকিটা পূরণ হচ্ছে খামারভিত্তিক মাছচাষ থেকে। দেশের প্রায় ৮.৭ লাখ হেক্টর পুকুর, খাল ও জলাভূমি এসব খামার গড়ে উঠেছে।
খামারভিত্তিক মাছচাষ দেশের মোট জিডিপির ২.৫৩ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপির ২২ শতাংশ। এটি প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ দুই কোটি মানুষের জীবিকার সংস্থান করছে। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অভ্যন্তরীণ মাছ উৎপাদনকারী দেশ।
দেশের পরিবারগুলোর জন্য এর সুফল কেবল অর্থনৈতিক নয়, পুষ্টিগতও বটে।
দেশের প্রাণিজ প্রোটিনের প্রায় ৬০ শতাংশ আসে মাছ থেকে। দৈনিক মাথাপিছু মাছ খাওয়ার পরিমাণ পৌঁছে গেছে ৬৭.৮ গ্রামে, যা সরকারের ৬০ গ্রামের লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। গত দশকে পাঙ্গাস ও তেলাপিয়ার মতো চাষ হওয়া মাছ গ্রামীণ পরিবারগুলোতে ইলিশ, রুই, কাতলার মতো দামী দেশি মাছের জায়গা দখল করে দিয়েছে।
সরকারি কর্মকর্তা ও মৎস্য বিশেষজ্ঞরা এর কৃতিত্ব দিয়েছেন নীতি, বিনিয়োগ ও উদ্যোক্তাদের সম্মিলিত প্রয়াসকে।

তাদের মতে, মৌসুমি নিষেধাজ্ঞায় ইলিশ উৎপাদন বাড়াতে সাহায্য করেছে। হ্যাচারিগুলো পোনার যোগান বাড়িয়েছে। আর বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) রোগ মোকাবিলায় উন্নত জাত ও পদ্ধতি চালু করেছে।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার দ্য ডেইলি স্টারকে বলেন, 'বাংলাদেশে মাছ চাষে সাফল্য এসেছে দূরদর্শী নীতি ও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগের সমন্বয়ে। উন্নত প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে, হ্যাচারি ও খাদ্য শিল্প সম্প্রসারিত হয়েছে, ইলিশ ধরা বন্ধের মতো সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে ফল পাওয়া গেছে।'
১৯৯০ ও ২০০০-এর দশকে আনা দ্রুত বর্ধনশীল মাছ—যেমন: পাঙ্গাস ও তেলাপিয়া—দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ মিল ও অক্সিজেনযুক্ত পরিবহন ট্যাংক মাছের ক্ষতি কমিয়েছে এবং ক্ষতিকর প্রিজারভেটিভ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কমিয়েছে।
ফরিদা আখতার বলেন, 'একই সময়ে চিংড়ি ও হিমায়িত মাছ রপ্তানির সুযোগ বাড়ায় উৎপাদনে প্রণোদনা তৈরি করেছে। সেইসঙ্গে সরকারি ভর্তুকি, ঋণ ও গবেষণা সহায়তায় কৃষকের ঝুঁকি কমেছে।'

বেসরকারি খাতও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে ৩১ লাখের বেশি কৃষক মাছচাষে যুক্ত।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, 'এসব সম্মিলিত উদ্যোগের কারণে ২০১০ সাল থেকে ২০ লাখ টনের বেশি উৎপাদন কেবল বাড়িয়েছে তাই নয়, গ্রামীণ জীবিকা, পুষ্টি নিরাপত্তা ও রপ্তানি সম্ভাবনাও বাড়িয়েছে। একই সঙ্গে টেকসই ও জলবায়ু সহনশীল মৎস্য উন্নয়নের ভিত্তি স্থাপন করেছে।'
ময়মনসিংহের একজন খামারি থেকে পরামর্শক হয়ে ওঠা এ বি এম শামসুল আলম তার শুরুর দিনগুলোর কথা স্মরণ করছিলেন। বলেন, 'নব্বইয়ের দশকের শুরুতে মাছচাষ শুরু করি। তখন বাংলাদেশে বাণিজ্যিক মাছচাষ ছিল একেবারেই শুরুর পর্যায়ে। তখন বাণিজ্যিক চাষ খুব একটা হতো না।'
তিনি বলেন, 'থাইল্যান্ড থেকে আনা পাঙ্গাস নিয়ে অনেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছিলেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে এই খাত অপরিণত ছিল। প্রথমে আমি চিংড়ি চাষ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু উৎপাদন এত কম হয়েছিল যে সেটা আর টেকসই হয়নি।"
'২০০২ সালের দিকে তেলাপিয়া চাষে মনোযোগ দিই। এটা অনেক বেশি কার্যকর প্রমাণিত হয়', বলেন তিনি।
শুরুর দিকে দেশে থাই কৈ ও তেলাপিয়ার পোনা আমদানিকারকদের মধ্যে অন্যতম শামসুল আলম। এগুলো তিনি কারওয়ান বাজারে রেকর্ড দামে বিক্রি করতেন। কৈ মাছের চাহিদা শেষ পর্যন্ত কমে গেলেও তেলাপিয়া বাজারে প্রধান মাছ হয়ে ওঠে।
তিনি বলেন, 'সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় মাছচাষ কেবল আর কৃষকের জীবিকা নয়, শিক্ষিত উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও পরিণত হয়েছে।'
বর্তমানে শামসুল আলম বিদেশের প্রকল্পে পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। তিনি ফিজিতে চিংড়ি ও তেলাপিয়া একসঙ্গে চাষ করা একটি পরীক্ষামূলক খামারে পরামর্শক হিসেবে রয়েছেন।

আঞ্চলিক কেন্দ্র
ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা দেশের সবচেয়ে বড় মাছ উৎপাদনকারী জেলায় পরিণত হয়েছে। প্রতিটি জেলায় বছরে তিন লাখ টনেরও বেশি মাছ উৎপাদন হয়।
ময়মনসিংহ জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন বলেন, 'এই জেলায় প্রায় এক লাখ মাছচাষি আছেন এবং তারা প্রায় ১৫ প্রজাতির মাছ চাষ করছেন। এর মধ্যে কিছু জাত বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই) উদ্ভাবিত। মূলত কার্পজাত মাছই এখানে চাষ হয়।'
তিনি বলেন, 'ভালুকা, মুক্তাগাছা ও ত্রিশালে মূলত পাঙ্গাস চাষ হয়। আর ফুলপুর ও তারাকান্দায় সিং, কৈ, পাবদা ও মাগুর চাষ বেশি হয়। অনেক কৃষক নানা জাতের মাছ মিশিয়েও চাষ করেন।'
তবে, রাজশাহীতে পরিবর্তনটা অপেক্ষাকৃত ধীর হলেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।
২০২৪ অর্থবছরে এই জেলায় ১ লাখ ১০ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, যার বাজারমূল্য ২ হাজার ৪০০ কোটি টাকা। প্রতিদিন প্রায় ৩০০ টন জীবন্ত মাছ এখান থেকে পাঠানো হয় মূলত ঢাকায়।
রাজশাহীতে শীর্ষ উৎপাদকদের মধ্যে আছে এসএস ফিশ ফার্ম। এর প্রতিষ্ঠাতা রসায়নের ছাত্র মো. গোলাম সাকলায়েন।
নব্বইয়ের দশকে এক মাছ সপ্তাহ প্রচারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি একটি পুকুর ইজারা নিয়ে মাছচাষ শুরু করেন। বর্তমানে তার খামার ৮০০ বিঘা জমিতে বিস্তৃত। সেখান থেকে প্রতিদিন ট্রাকে ১৫-২০ লাখ টাকার মাছ বিভিন্ন বাজারে পাঠানো হয়।

অসম উন্নতি
মৎস খাতের এই উত্থান সবার জন্য সমান সুফল বয়ে আনেনি। লবণাক্ততা ও বন্যার কারণে খুলনা ও সাতক্ষীরার কৃষকদের ঠেলে দিয়েছে কাঁকড়া ও লবণসহিষ্ণু মাছ চাষের দিকে।
রাজশাহীর গোদাগারীর চাষি রফিকুল ইসলাম জানান, গত এক দশকে মাছের খাদ্যের দাম দ্বিগুণ হয়েছে। ৬০০-৭০০ টাকা থেকে বেড়ে প্রতি বস্তা খাবারের দাম হয়েছে ১,৪০০-১,৫০০ টাকা। চুন ও ওষুধসহ অন্যান্য খরচও বেড়েছে।
রফিকুল ইসলাম বলেন, 'এ বছর দেড়লাখ টাকা খরচ করেছি শুধু চুন ও অন্যান্য উপকরণ কিনে পুকুর ভালো রাখার জন্য। কিন্তু কাজ হয়নি।'
তার ধারণা, ছোট মাছচাষিদের ৮০ শতাংশই প্রতিবছর লোকসান গুনে। বড় বিনিয়োগ করা চাষিরা দীর্ঘ সময় মাছ ধরে রাখতে পারে, ফলে ভালো দাম পায়। ছোট বিনিয়োগকারীরা বাধ্য হয় আগেভাগেই বিক্রি করতে, ফলে লাভ খুব সামান্য হয়।
বিশেষজ্ঞরা অবশ্য সতর্ক করেছেন চাষের মাছের পুষ্টিগুণ নিয়ে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, 'গবেষণায় দেখা গেছে, খামারের মাছের পুষ্টিগুণ কম হয় কিছুটা নিম্নমানের খাবার খাওয়ানোর কারণে।'
তিনি বলেন, 'অনেক খামারের মাছে ভারী ধাতু ও অ্যান্টিবায়োটিকও পাওয়া গেছে। দূষিত নদীর মাছেও একই ঝুঁকিতে থাকে। কারণ, পানির বিষাক্ত উপাদান সরাসরি তাদের শরীরে প্রবেশ করে।'
মৎস কর্মকর্তারা বলছেন, তারা এ সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন।
মৎস্য উপদেষ্টা ফরিদা আখতার জানান, মৎস সম্প্রসারণ বিভাগ এখন 'সুন্দর মাছচাষ পদ্ধতি' ও পরিবেশবান্ধব পুকুর ব্যবস্থাপনা প্রচার করছে।
তিনি বলেন, 'এটা ঠিক যে মাছের খাদ্যের দাম বেড়ে যাওয়ায় কৃষক চাপে পড়ছেন। এ জন্য সরকার স্থানীয় খাদ্য উৎপাদনকে উৎসাহিত করছে, বিকল্প উপাদানে গবেষণা করছে এবং খরচ কমাতে ক্লাস্টারভিত্তিক ক্রয় ব্যবস্থা চালু করছে।'

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব
স্থানীয় বাণিজ্যিক মাছচাষের জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসছে পরিবেশ থেকে।
অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম বলেন, 'সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, এ বছর মোট মাছ উৎপাদন আড়াই শতাংশ বেড়েছে। অথচ ইলিশ উৎপাদন ৭ শতাংশ ও চিংড়ি ১৮ শতাংশ কমেছে।'
২০২৪ সালে বৃষ্টি দেরিতে হওয়ায় তাপমাত্রা বেড়েছে, আর চরম আবহাওয়া মাছের খামারগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। বরেন্দ্র অঞ্চলে আগে যেখানে পুকুরে নয় মাস পানি থাকত, এখন পাঁচ মাসেই শুকিয়ে যায়। যশোরে ভারী বৃষ্টিতে মাঠ প্লাবিত হয়েছে। হাওর অঞ্চলে বজ্রপাত বেড়ে গেছে, এতে প্রচুর মাছ মারা যাচ্ছে।
মৎস উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, 'জলবায়ু পরিবর্তন ইতোমধ্যেই দেশের মৎস্য খাতকে প্রভাবিত করছে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় সরকার জলবায়ু সহনশীল পদ্ধতির প্রচার করছে, লবণ-সহিষ্ণু ও তাপ-সহিষ্ণু মাছের ওপর গবেষণায় সহায়তা দিচ্ছে এবং ব্লু ইকোনমি কাঠামোর আওতায় আগাম সতর্কবার্তা ব্যবস্থা জোরদার করছে।'
তবে অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম সতর্ক করেছেন, অভিযোজন প্রচেষ্টা এখনো খণ্ডিত এবং এর জন্য পর্যাপ্ত অর্থায়ন নেই। মৎস্য খাতের জন্য বাংলাদেশ এখনো বড় কোনো আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল পায়নি।
তিনি বলেন, 'মৎস্য অধিদপ্তরের বেশিরভাগ প্রকল্প ছোট আকারের। এগুলো সচেতনতা বা পাইলট প্রকল্পেই সীমাবদ্ধ। পিকেএসএফ গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড প্রকল্পের আওতায় কাঁকড়ার ওপর পরীক্ষা শুরু করেছে, আর স্থানীয় সরকার বিভাগ হাওর এলাকায় কাজ করছে।'
খামারভিত্তিক চাষ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগও বেড়েছে। খবর পাওয়া যায় যে, মাছ সংরক্ষণে ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার করা হচ্ছে এবং রোগ প্রতিরোধে অতিরিক্ত অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করা হচ্ছে।
আন্তর্জাতিক ক্রেতারাও এগুলো খেয়াল করেছে। একসময় বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি আয়কারী চিংড়ি বারবার ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে মান নিয়ন্ত্রণ ত্রুটির কারণে।
মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুর রউফ বলেন, 'মান নিয়ন্ত্রণ এখন অগ্রাধিকার। চিংড়ির বাইরে আমরা তেলাপিয়া, পাঙ্গাস, কৈ, কাঁকড়া ও অন্যান্য জীবন্ত মাছ আন্তর্জাতিক বাজারে পাঠানোর চেষ্টা করছি। আন্তর্জাতিক মানের ল্যাব ও ট্রেসেবিলিটি সিস্টেম তৈরি হচ্ছে।'
তার মতে, উন্নত ব্র্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশ এক দশকের মধ্যে রপ্তানি আয় দ্বিগুণ করতে পারে।
তবে, শিল্প বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছেন যে চাষের মাধ্যমে উৎপাদনের পাশাপাশি ঝুঁকিও বাড়াছে। খাদ্যের চাহিদা বেড়েছে, রাসায়নিক ব্যবহারের প্রবণতা ও রোগ ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।
রাজশাহীর সাকলায়েন বলেন, 'আমাদের আর পুকুর দরকার নেই। দরকার খাদ্য নিরাপত্তা ও পরিবেশগত মানদণ্ডে কঠোর নজরদারি।'
মৎস কর্মকর্তারা জোর দিয়ে বলেন, এখন টেকসই উন্নয়ন হতে হবে নীতির কেন্দ্রে। ক্লাস্টারভিত্তিক চাষ, সনদপ্রদান ব্যবস্থা, সমন্বিত মডেল ও জীবাণুমুক্ত পুকুর ব্যবস্থাপনা প্রচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি জলবায়ু সহনশীল প্রজাতির ওপর গবেষণাও চলছে।
শামসুল আলমের মতো কৃষকের পরিস্কার বার্তা হলো, 'জাত নির্বাচন, খাদ্য উন্নয়ন ও বিপণনের চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। কিন্তু অগ্রযাত্রা থেকে দেখা যাচ্ছে যে কীভাবে উদ্ভাবন ও উদ্যোগ মাছের বিপ্লব ঘটিয়েছে। এখন সময় এসেছে কৃষককে নিরাপদ মাছ উৎপাদনে উৎসাহিত করার, যেখানে মানুষের জন্য ক্ষতিকর অ্যান্টিবায়োটিক ও রাসায়নিক কম ব্যবহার হবে। এটা সরকারি সংস্থাগুলোর দায়িত্ব।'
আগামীর চ্যালেঞ্জ কেবল মাছ উৎপাদন বাড়ানো নয়, বরং তা টেকসইভাবে করা এবং ছোট কৃষক ও ভঙ্গুর প্রতিবেশ উভয়কেই রক্ষা করে।
অধ্যাপক মনিরুল ইসলাম বলেন, 'ভবিষ্যতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাছের চাহিদাও বাড়বে। কিন্তু, প্রশ্ন হলো, উৎপাদন কি জলবায়ু সহনশীল ও টেকসই করা সম্ভব হবে?'
আপাতত পুকুর ভরা আছে, বাজারেও সরবরাহ পর্যাপ্ত। আগামী দিনে বাংলাদেশ এই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারবে কি না, তা নির্ভর করবে কতটা দক্ষতার সঙ্গে প্রবৃদ্ধি ও সহনশীলতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা যাবে তার ওপর।





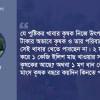





Comments