সান্ধ্য কোর্স: বিশ্ববিদ্যালয় যখন পণ্য বেচা-কেনার হাট

সান্ধ্য কোর্স নিয়ে অনেক কথা বার্তা চলছে। আমেরিকার অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে এটা আছে, নতুন কিছু নয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই ধরনের অতিরিক্ত কিছু প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফ্যাকাল্টি এবং বিভাগের জন্য রিসোর্স তৈরি করে। বিজনেস ফ্যাকাল্টির এই ধরনের প্রোগ্রামের জনপ্রিয়তা বেশি। আজকাল আমেরিকার আইভি লিগ থেকে শুরু করে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ধরনের প্রোগ্রাম রয়েছে। প্রচুর এমবিএ প্রোগ্রাম আছে, এক্সিকিউটিভ এমবিএ, ইভনিং এমবিএ এবং অনলাইন এমবিএ। ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস অস্টিনের এমবিএ প্রোগ্রাম ডালাস শহরে আছে। এদের ইভনিং এমবিএ প্রোগ্রামও ডালাসে আছে। প্রতি সেমিস্টারে এক্সিকিউটিভ এমবিএর টিউশন ফি প্রায় ২৪ হাজার ডলার। কাজেই দেড় থেকে দুই বছরে টিউশন ফি কত হবে নিজেই হিসাব করে বের করা যায়।
যেকোনো বড় এবং নামি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সব প্রোগ্রাম অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু এই প্রোগ্রামগুলোতে কোনো দুর্বল ছাত্র ভর্তি হতে পারে না। বাংলাদেশে অনেকে সান্ধ্য কোর্সের ছাত্রদের অ্যালামনাইয়ের মর্যাদা দিতেও ইচ্ছুক নয়। সেটার যদিও কিছু ভিত্তি আছে, কারণ ভর্তি ফিল্টারটা যেহেতু নেই। কিন্তু আমেরিকার নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসব প্রোগ্রামে ভর্তি হতে হলে তাৎপর্যপূর্ণ কাজ এবং উচ্চপদে কাজ করার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকতে হয়। যাকে তাকে ডিগ্রি দেওয়া হয় না। তবে শিক্ষকদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য এই প্রোগ্রামগুলো তৈরি করা হয় না। এর ফলে বিভাগগুলো নতুন বৃত্তি দিতে পারে। গবেষণা এবং শিক্ষক নিয়োগের সময় নতুন শিক্ষককে কিছু অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি, ভালো কম্পিউটার দিতে পারে। এছাড়া সফল মানুষদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারে এই ধরনের ডিগ্রি দিয়ে। আগে বিজ্ঞানে এই ধরনের প্রোগ্রাম ছিল না। আজকাল আমেরিকার বিভিন্ন স্কুলগুলোতে উচ্চ টিউশনের বায়োমেডিক্যাল সায়েন্সের কিছু মাস্টার্স প্রোগ্রাম আছে। আগে বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিস্ট্রির প্রোগ্রামগুলতে পিএইচডি ছাত্র ছাড়া মাস্টার্সের কোনো ছাত্র ভর্তি করা হতো না। এখন করা হচ্ছে, কারণ এরা সম্পূর্ণ টিউশন দিয়ে পড়ে তাতে বিভাগের লাভ। কিন্তু মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দেওয়া হয় না।
এবার আসছি সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয়ে। এই প্রোগ্রামগুলোর কোর্স কে পড়ায়? প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের তাদের কাজের নিয়মাবলী দেওয়া থাকে। যেমন আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে/বিভাগে এটা ৪০ ভাগ পড়ানো, ৪০ ভাগ গবেষণা এবং ২০ ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্ভিস, মানে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কমিটিতে থেকে কাজ করা। সব গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এই নিয়মেই চলে। টিচিং বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার এটা ভিন্ন। সেখানে পড়ানোর ভাগটা বেশি। মাঝে মধ্যে কোনো ফ্যাকাল্টির খুব বেশি ফান্ডিং থাকলে টিচিং অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। তবে বিজ্ঞানে আমাদের কোর্স লোড হচ্ছে ১+১, অর্থাৎ, প্রতি সেমিস্টারে একটা কোর্স। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে এটা ২+২। বিশ্ববিদ্যালয় ভেদে এটা ভিন্ন হতে পারে। আমেরিকাতে একাডেমিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরি হচ্ছে নয় মাস, এবং সামারে শিক্ষকেরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনো বেতন পায় না। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই নয় মাসের বেতন অন্যান্য চাকরির সারা বছরের বেতনের সমান। সামারে, শিক্ষকরা অতিরিক্ত বেতন নিতে পারেন তাদের গ্রান্ট থেকে অথবা সামারে অতিরিক্ত কোর্স পড়িয়ে। আমেরিকাতে গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষকই সামারে পড়াতে চান না। শিক্ষক যদি গবেষণায় সক্রিয় হন, সামারের তিন মাস তিনি সম্পূর্ণ গবেষণায় মনোযোগ দিতে পারেন।
সান্ধ্য কোর্সগুলো নিয়মিত সেমিস্টারে অফার করা হয়। বিভাগ চাইলে, শিক্ষক সার্ভিস রুলের অতিরিক্ত সময় দিলে কোর্স প্রতি তাকে টাকা প্রদান করতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই কোর্সগুলোর জন্য অতিরিক্ত অ্যাডজাঙ্কট প্রফেসর নিয়োগ দেওয়া হয়। আমেরিকাতে গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষকই পয়সা দিলেও অতিরিক্ত কোন কোর্স পড়াতে চান না। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এটা ভিন্ন, শিক্ষকদের বেতন এমনিতেই কম, এটা তাদের একটা অতিরিক্ত আয়।
সান্ধ্য কোর্স খারাপ কিছু নয়। এটা কর্মজীবীদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। আমেরিকাতে অনেক ক্ষেত্রে এর টিউশন ফি কোম্পানি থেকে দেওয়া হয়। এর কারণ হচ্ছে তারা দক্ষ কর্মীদের তাদের কোম্পানিতে রাখতে চায়। কাজেই এতে ভর্তির পদ্ধতিটা ঠিক রাখতে পারলে, এবং সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম করতে পারলে, এটা বিভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত রিসোর্স তৈরি করতে সাহায্য করবে। মান বজায় রেখে এটা করতে পারলে কোন সমস্যা দেখি না। রেগুলার শিক্ষকদের মূল্যায়নের মধ্যে রাখলে একটা চেক এন্ড ব্যাল্যান্স থাকবে কাজেই দিনের কোর্সগুলোতে সময় না দেওয়ার প্রশ্নটা আসবে না। পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিভিন্ন ভাবে রিসোর্স তৈরি করতে চেষ্টা করে। অনেকে গবেষণার জন্য গিফট মানিও দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক নামের প্রফেসরশিপও আছে, তাতে প্রফেসরদের অতিরিক্ত গবেষণার অর্থ আসে। এছাড়া রিসোর্স তৈরি করার জন্য অ্যালামনাই ডোনেশন অনেক কাজে লাগে। আমি ওয়াশিংটন স্টেট থেকে পিএইচডি করেছি। প্রায়ই ইমেইল এবং কল পাই যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য কিছু ডোনেশন করি। আমেরিকার প্রেসিনেন্সিয়াল নির্বাচনে ছোট ছোট ডোনেশনে প্রচুর টাকা প্রার্থীরা উঠিয়ে আনেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যদি সবাই অল্প পরিমাণে ডোনেশন দেয়, তা দিয়ে ল্যাব এমনকি ছাত্রদের জন্য নতুন হল তৈরি করা সম্ভব বলে আমি মনে করি। অ্যালামনাই সংযোগের মাধ্যমে এগুলো শুরু করা অত্যন্ত জরুরি।
আসলে বিশ্ববিদ্যালয় কী এবং কেন এত বছরেও আমরা বুঝতে পারছি না। এটা বুঝতে না পারাটা সত্যিই দুঃখজনক।
সাইফুল মাহমুদ চৌধুরী: যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাস এট আরলিংটনের রসায়ন এবং প্রাণ রসায়ন বিভাগে অধ্যাপনা করেন।
(দ্য ডেইলি স্টারের সম্পাদকীয় নীতিমালার সঙ্গে লেখকের মতামতের মিল নাও থাকতে পারে। প্রকাশিত লেখাটির আইনগত, মতামত বা বিশ্লেষণের দায়ভার সম্পূর্ণরূপে লেখকের, দ্য ডেইলি স্টার কর্তৃপক্ষের নয়। লেখকের নিজস্ব মতামতের কোনো প্রকার দায়ভার দ্য ডেইলি স্টার নিবে না।)




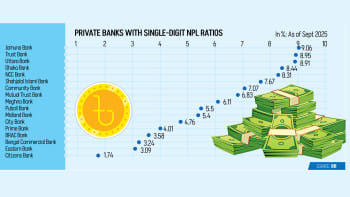
Comments