‘আল্লাহ তুই দেহিস’: অসহিষ্ণু সমাজের অসহায় প্রতিচ্ছবি

ময়মনসিংহের তারাকান্দার কাশীগঞ্জ বাজারের এক কোণে মাটিতে ফেলে ৭০ বছর বয়সী বাউল সাধক হালিম উদ্দিন আকন্দকে যখন কয়েকজন মিলে চেপে ধরেছিল, তখন তাদের হাতে ছিল কাঁচি আর ক্লিপার। অসহনীয় অপমানের মুখে দাঁড়িয়ে, শারীরিক প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়ে হালিম উদ্দিনের মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল কয়েকটি মাত্র শব্দ—আল্লাহ, তুই দেহিস।
এই আর্তনাদ কোনো সাধারণ অভিযোগ নয়। একবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে একজন প্রান্তিক মানুষের শেষ আশ্রয়, যখন সমাজ ও রাষ্ট্র তাকে সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়।
এ দৃশ্য কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং এটি আমাদের সমাজের গভীরে ছড়িয়ে পড়া অসহিষ্ণুতা, বিচারহীনতার সংস্কৃতি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার ওপর এক নির্মম আক্রমণের প্রতিচ্ছবি।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওটি আমাদের সম্মিলিত বিবেককে এক কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। আমরা এমন এক সমাজে বাস করছি, যেখানে একজন মানুষের ৩৭ বছরের সাধনা, তার বিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের প্রতীক—জট ধরা চুল—কেটে ফেলাটা কেবল সম্ভবই নয়, বরং সেই পাশবিকতাকে ভিডিও করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দেওয়া হয় বাহবা কুড়ানো ও টাকা কামানোর জন্য।
এই ঘটনা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, আমরা কতটা ভয়ংকর এক সামাজিক অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এটি কেবল একজন হালিম উদ্দিনের অপমান নয়, এটি আমাদের বহুত্ববাদী চেতনার কফিনে ঠোকা আরও একটি পেরেক।
সহিংসতার নতুন পণ্য 'ভিউ বাণিজ্য'
এই চুল কাটার পেছনে যে চালিকাশক্তি কাজ করছে তা হলো, এক নির্মম ও নির্লজ্জ 'ভিউ বাণিজ্য'। ফেসবুক ও ইউটিউবের মতো প্ল্যাটফর্মগুলো এখন আর কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এগুলো এক বিশাল অর্থনীতির ক্ষেত্রও। যেখানে 'কনটেন্ট' হলো মুদ্রা। এই মুদ্রার মান নির্ধারিত হয় ভিউ, লাইক আর শেয়ারের সংখ্যা দিয়ে।
বাংলাদেশের মতো দেশগুলোতে, যেখানে বিজ্ঞাপনের আয় তুলনামূলকভাবে কম, সেখানে কনটেন্ট নির্মাতাদের লাখো ভিউয়ের জন্য মরিয়া হয়ে উঠতে দেখা যায়। আর এই ভিউয়ের সহজতম পথ হলো—উত্তেজনা, বিতর্ক ও অন্যের অবমাননাকে পণ্যে রূপান্তর করা।
ভিডিওটি দেখলেই বোঝা যায়, হালিম উদ্দিনের চুল কাটার ঘটনাটি ছিল পূর্বপরিকল্পিত। একজন পুরো ঘটনাটি ভিডিও করছিলেন। তারা জানতেন, এই ধরনের ভিডিওর একটি 'বাজারমূল্য' আছে।
ভিডিওটি আপলোড হওয়ার পর দর্শকের একাংশ যখন 'সমাজ সংস্কার'-এর নামে এই কাজের প্রশংসা করে, অন্য একটি অংশ যখন তীব্র সমালোচনা করে। তখন উভয়পক্ষ অজান্তেই নির্মাতার উদ্দেশ্য সফল করে দেয়।
এই বিতর্ক ভিডিওর 'এনগেজমেন্ট' বাড়ায়, অ্যালগরিদম সেটিকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয় এবং দিন শেষে নির্মাতার পকেটে কিছু টাকা আসে। অন্যের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করে অর্জিত এই অর্থ রক্তমাখা টাকারই নামান্তর।
এই ভিউ বাণিজ্যের সবচেয়ে কপট ও বিপজ্জনক রূপটি হলো 'মানবিকতার' মুখোশ। 'মাহবুব ক্রিয়েশন' বা 'স্ট্রিট হিউম্যানিটি অব বাংলাদেশ'-এর মতো কিছু পেজ বছরখানেক ধরে প্রায়শই গৃহহীন, মানসিক ভারসাম্যহীন বা জটধারী বাউলদের ধরে তাদের সম্মতি ছাড়াই চুল-দাড়ি কেটে, গোসল করিয়ে ভিডিও তৈরি করে। তাদের ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে নিয়মিত এসব ভিডিও প্রকাশ করা হয়।
তারা এই কাজকে 'মহৎ মানবিক উদ্যোগ' হিসেবে প্রচার করে। কিন্তু এটি মানবিকতা নয়, চরম সুবিধাবাদ। একজন অসহায় মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ, আত্মপরিচয় ও সম্মতির অধিকারকে অগ্রাহ্য করে, তার দুর্দশাকে পুঁজি করে ডিজিটাল পণ্য তৈরি করা—এটি এক নতুন ধরনের অপরাধ, যাকে 'পারফরম্যাটিভ ভায়োলেন্স' বা প্রদর্শনমূলক সহিংসতা বলা যায়।
এখানে সহিংসতার উদ্দেশ্য শাস্তি নয়, বরং সহিংসতাকে দর্শনযোগ্য করে তোলা। দর্শকরা যখন এই ভিডিও দেখি, লাইক বা শেয়ার করি, তখন আমরাও এই অপরাধের নীরব অংশীদার হয়ে যাই। অন্যদিকে যারা এই কাজটি করছে, তারা কেবল অসহায় মানুষকেই লক্ষ্য বানাচ্ছে, কোনো সামর্থ্যবান, ক্ষমতাশালী বা প্রভাবশালী কারও মাথায় জটা চুল থাকলেও সেটা কাটার সাহস তারা করছে না।
রাষ্ট্রের নীরবতা ও বিচারহীনতার সংস্কৃতি
আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংগঠনগুলো একাধিকবার বলেছে, জোরপূর্বক চুল কেটে দেওয়া একটি গুরুতর ফৌজদারি অপরাধ এবং এটি সংবিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
আমাদের সংবিধানের ৩১, ৩২ ও ৩৫ নম্বর অনুচ্ছেদ প্রতিটি নাগরিককে আইনের আশ্রয়, ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নিষ্ঠুর ও অমানবিক আচরণ থেকে সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার দিয়েছে। কিন্তু এই সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির সঙ্গে মাঠের বাস্তবতার মধ্যে ফারাক আকাশ-পাতাল।
হালিম উদ্দিনের ঘটনায় স্থানীয় পুলিশের ভূমিকা ছিল হতাশাজনক। তাদের বক্তব্য ছিল, ভুক্তভোগী অভিযোগ করলে তারা ব্যবস্থা নেবেন। এটি দায়িত্ব এড়ানোর একটি ক্লাসিক উদাহরণ। যখন একটি ফৌজদারি অপরাধ জনসমক্ষে ঘটে এবং তার ভিডিও প্রমাণ দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে, তখন পুলিশের দায়িত্ব স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা রুজু করা। প্রান্তিক, ভীত ও বিচারব্যবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ একজন মানুষের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক অভিযোগের আশা করাটা ন্যায়বিচারকে বাধাগ্রস্ত করারই শামিল।
এই প্রাতিষ্ঠানিক নিষ্ক্রিয়তা অপরাধীদের কাছে একটি পরিষ্কার বার্তা পৌঁছে দেয়, তোমরা যা খুশি করতে পারো, বিশেষ করে যদি ভুক্তভোগী দুর্বল হয়, তোমাদের কিছুই হবে না।
এর ঠিক বিপরীত চিত্র আমরা দেখেছিলাম ২০২১ সালে সিরাজগঞ্জের রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায়। সেখানে একজন শিক্ষক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ১৪ জন ছাত্রের চুল কেটে দিয়েছিলেন। সেই ঘটনায় গণমাধ্যমের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেছিলেন।
আদালত শুধু ঘটনার বৈধতা নিয়েই প্রশ্ন তোলেননি, বরং ভুক্তভোগীদের জন্য ক্ষতিপূরণ ও ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে গাইডলাইন তৈরির কথাও বলেছেন।
বিচার বিভাগের এই সক্রিয়তা প্রশংসার যোগ্য, কিন্তু এটি একটি বড় কাঠামোগত সংকটকেও তুলে ধরে। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য যদি আমাদের বারবার উচ্চ আদালতের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়, তবে বুঝতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে আইনের শাসন কতটা ভঙ্গুর।
অসহিষ্ণুতার সামাজিক শেকড়
আইন ও বিচারহীনতার বাইরেও আমাদের তাকাতে হবে সমাজের গভীরে। কেন একজন হালিম উদ্দিনকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু হতে হয়? কারণ তিনি 'ভিন্ন'। তার বাউল বেশ, তার জট ধরা চুল সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে 'অস্বাভাবিক' বা 'বিচ্যুত' মনে হতে পারে। এই ভিন্নতাকে সহ্য করতে না পারার অক্ষমতাই হলো অসহিষ্ণুতা।
সমাজতাত্ত্বিকভাবে, চুল কেটে দেওয়া ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যকে মুছে ফেলে তাকে সমষ্টির অনুগামী করার একটি প্রতীকী প্রচেষ্টা। এটি ব্যক্তির ওপর গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার এক আদিম কৌশল।
যারা এই কাজগুলো করে, তারা প্রায়শই নিজেদের 'সমাজ সংস্কারক' হিসেবে পরিচয় দেয়। তারা আইন নিজের হাতে তুলে নেয় এবং এক ধরনের 'নৈতিক পুলিশগিরি' প্রতিষ্ঠা করতে চায়। এই মানসিকতা অত্যন্ত বিপজ্জনক, কারণ এটি সমাজে বিভেদ ও ঘৃণা ছড়ায় এবং ভিন্ন জীবনধারা ও বিশ্বাসের মানুষের জন্য একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে।
যখন রাষ্ট্র এই 'নৈতিক পুলিশদের' বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়, তখন রাষ্ট্র পরোক্ষভাবে তাদের কর্মকাণ্ডকে বৈধতা দেয়।
উত্তরণের পথ কোথায়?
এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য একটি বহুমাত্রিক ও সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।
প্রথমত, রাষ্ট্রকে তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে যেকোনো মূল্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এ ধরনের ঘটনায় অভিযোগের অপেক্ষা না করে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের এবং দ্রুততম সময়ে অপরাধীদের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।
দ্বিতীয়ত, ফেসবুক-ইউটিউবের মতো ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোকে তাদের দায়বদ্ধতা স্বীকার করতে হবে। তারা কেবল প্রযুক্তিনির্ভর নিষ্ক্রিয় মাধ্যম নয়। তাদের ব্যবসায়িক মডেল ও অ্যালগরিদম যখন ঘৃণাত্মক ও অবমাননাকর কনটেন্টকে পুরস্কৃত করে, তখন তাদেরও এই অপরাধের দায় নিতে হবে।
বাংলাদেশ সরকারের উচিত এই প্ল্যাটফর্মগুলোর ওপর চাপ সৃষ্টি করা, যাতে তারা এ ধরনের কনটেন্ট দ্রুত অপসারণ করে এবং নির্মাতাদের স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ ও মনিটাইজেশন বাতিল করে।
তৃতীয় ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো সামাজিক প্রতিরোধ ও সচেতনতা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা, পরিবার ও সামাজিক পরিসরে পরমতসহিষ্ণুতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার গুরুত্ব শেখাতে হবে। ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন একটি সভ্য সমাজের ন্যূনতম শর্ত। নাগরিক সমাজ, গণমাধ্যম ও সচেতন ব্যক্তিদের এ ধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে আওয়াজ তুলতে হবে।
হালিম উদ্দিনের আর্তনাদ 'আল্লাহ তুই দেহিস' আমাদের জন্য একটি সতর্কবার্তা। এটি আমাদের সমাজের সম্মিলিত ব্যর্থতার এক শক্তিশালী দলিল। আমরা যদি এখনই এই অসহিষ্ণুতা এবং বিচারহীনতার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে রুখে না দাঁড়াই, তাহলে এমন আরও অনেক হালিম উদ্দিনকে নীরবে অপমান সহ্য করে কেবল আকাশের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে।
একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে এটা আমাদের জন্য চরম লজ্জার। আমরা এমন একটি সমাজ চাই, যেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজস্ব পরিচয়, বিশ্বাস ও জীবনধারা নিয়ে নিরাপদে এবং মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে পারবে। সেই সমাজ গড়ার দায়িত্ব আমাদের সকলের।
তানজিল রিমন; সাংবাদিক ও শিশুসাহিত্যিক








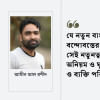
Comments